বিদ্রোহী কবিতা ও প্রাসঙ্গিক কথা
- প্রকাশিত: শনিবার, ২ আগস্ট, ২০২৫
- ২৫০ বার পড়া হয়েছে
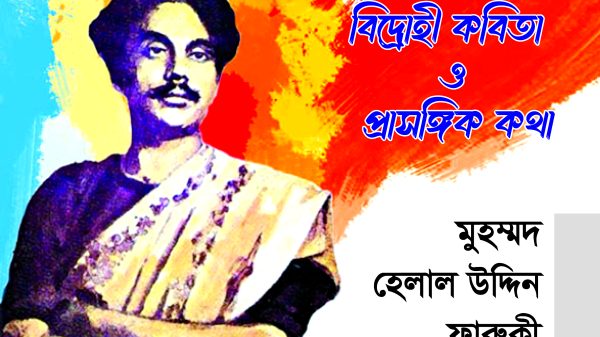
মুহম্মদ হেলাল উদ্দিন ফারুকী
যে কবিতাটি নজরুলকে তাঁর কবি-জীবনের শুরুতেই খ্যাতির চরম শিখরে নিয়ে যায়, তার নাম ‘বিদ্রোহী’। নজরুল দ্রোহ-ভাবাপন্ন আরো অনেক কবিতা লিখলেও শুধু এক ‘বিদ্রোহী’ কবিতার জন্যই তিনি বাঙালির চিরকালের ‘বিদ্রোহী কবি’।এই বছরটি বিদ্রোহী কবিতার ১০৪ বছর পূর্তি। ২০২৬ সালে কবিতাটির ১০৫ বছর পূর্তি হবে। এরকম অসাধারণ শব্দচয়ন, স্বতন্ত্র ভাষারীতি ও অভিনব ছন্দের গাঁথুনিতে রচিত বিদ্রোহ-দৃপ্ত, রুদ্ররোষে বলীয়ান কবিতা বাংলা সাহিত্যে আর একটিও নেই। এমনকি বিশ্বসাহিত্যেও এর তুলনা খুঁজে পাওয়া ভার।
ভারতীয় উপমহাদেশ তখন ব্রিটেনের পরাধীন। প্রথম মহাযুদ্ধ সবেমাত্র শেষ হয়েছে। নজরুল তাঁর সৈনিক জীবন সমাপ্ত করে ফিরে এসেছেন কলকাতায়। বেছে নিয়েছেন সাহিত্য চর্চা, সাংবাদিকতা ও রাজনৈতিক আন্দোলনের এক ত্রিমুখী জীবন। ব্রিটিশবিরোধী অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারতবর্ষ তখন টালমাটাল।শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হকের ‘নবযুগ’ পত্রিকায় তিনি নিয়মিত সাংবাদিকতা শুরু করলেন। তখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। একই সাথে তিনি ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন।এমনই এক উত্তাল সময়ে ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে নজরুল রচনা করেন তাঁর কালজয়ী কবিতা ‘বিদ্রোহী’। বিভিন্ন তথ্যসূত্র মতে, কলকাতার তালতলা লেনের ৩/৪ সি বাড়িটি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিদ্রোহী কবিতার আঁতুড়ঘর। দ্বিতল এই বাড়িটিতে বসে কবি লিখেছিলেন রক্তে দোলা জাগানিয়া ‘বল বীর.. চীর উন্নত মম শির।’
কবিতার প্রতিটি পঙক্তি যেন শরীরের রক্ত শুদ্ধ করে আওয়াজ তোলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহের দামামা বাজায় প্রতি মুহূর্তে, আজও এই কবিতার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। নেইকোনো বিতর্ক। কবিরভাষায়- আমি ঝঞ্ঝা, আমি ঘূর্ণি/আমি পথ-সমুখে যাহা পাই; যাই চূর্ণি/ আমি নৃত্য-পাগল ছন্দ/ আমি আপনার তালে নেচে যাই, আমি মুক্ত জীবনানন্দ/ আমি হাম্বীর, আমি ছায়ানট, আমি হিন্দোল/ আমি চল-চঞ্চল, ঠমকি ছমকি/পথে যেতে যেতে চকিত চমকি-
বিদ্রোহী কবিতা রচনাকাল এবং সময় নিয়ে বিস্তর বিতর্ক আছে। অপরদিকে বিদ্রোহী কবিতা প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল সে বিষয়েও দ্বন্দ্ব আছে আজও।তবে বিতর্ক যাই থাকুক, কলকাতার তালতলা লেনের ৩/৪সি লেনের বাড়িটিরনিচ তলার কোন এক অন্ধকার ঘরে লন্ঠন জ্বালিয়ে কবি তাঁর চিন্তার ভ্রূণ কলমের কালির মধ্যদিয়ে সাদা পৃষ্ঠায় ঢেলে গিয়েছিলেন, বর্ণমালায় একে একে গেঁথে গিয়েছিলেন বিদ্রোহী কবিতা- সেটা নিয়ে বিতর্কে অংশ নেওয়া নজরুল ইসলামের সমসাময়িক প্রায় সবাই একমত রয়েছেন।
কবিতাটি কোথায়, কখন রচিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গেকবিবন্ধু কমরেড মুজফফর আহমেদএক স্বাক্ষাতকারেবলেছেন, ‘এই ঘরেই (কলকাতার তালতলা লেনের ৩/৪সি লেনের বাড়ি) কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিদ্রোহীকবিতা লিখেছিল। সে কবিতাটি লিখেছিল রাত্রিতে। রাত্রির কোন সময়ে তা আমি জানিনে। রাত ১০টার পরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলেম। সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধুয়ে আমি বসেছি এমন সময় নজরুল বলল, সে একটি কবিতা লিখেছে। পুরো কবিতাটি সে তখন আমায় পড়ে শোনাল। বিদ্রোহীকবিতার আমিই প্রথম শ্রোতা।’ মুজফফর আহমদ জানিয়েছেন, নিজের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের কারণেই কবিতাটি শুনে তিনি কোনো উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেননি। এতে নজরুল মনে মনে আহত হয়েছেন নিশ্চয়ই। কবিতাটির রচনার সময় নিয়ে মুজফফর আহমদ আবার বলেছেন, ‘আমার মনে হয় নজরুল ইসলাম শেষ রাত্রে ঘুম থেকে উঠে কবিতাটি লিখেছিল। তা না হলে এত সকালে সে আমায় কবিতা পড়ে শোনাতে পারত না। তাঁর ঘুম সাধারণত দেরীতেই ভাঙত, আমার মতো তাড়াতাড়ি তাঁর খুব ভাঙত না।’ মুজফফর আহমদ আরও জানিয়েছেন, নজরুল সম্ভবত প্রথমে কবিতাটি পেনসিলে লিখেছিলেন।আবার, নজরুল গবেষকসুশীল কুমার সেনগুপ্তের মতে, কবিতাটি(বিদ্রোহী) রচিত হয়েছিল ১৯২১ সালের দুর্গাপূজার কাছাকছি সময়ে।
‘বিদ্রোহী’ কোন পত্রিকায় প্রথম ছাপা হয়েছিল সে নিয়েও বিতর্ক আছে। নজরুল রচনাবলীর (বাংলা একাডেমি) সম্পাদক আবদুল কাদির প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ পরিচয়ে জানিয়েছেন, ‘বিদ্রোহী ১৩২৮ কার্তিকে ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যক ‘মোসলেম ভারত’-এ বাহির হইয়াছিল। ১৩২৮ সালের ২২শে পৌষের সাপ্তাহিক বিজলীতে এবং ১৩২৮সালের মাঘের‘প্রবাসী’তে উহা সংকলিত হইয়াছিল।’ আবদুল কাদির এ তথ্যও জানিয়েছেন যে ‘মোসলেম ভারতে’ প্রকাশিত ‘বিদ্রোহী’ কবিতায় আরও কয়েকটি চরণ ছিল, যেগুলো পরে পরিত্যক্ত হয়েছে। কিন্তুকবিবন্ধু মুজফফর আহমদ বলেছেন, ‘বিদ্রোহী’ প্রথমে সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকায় ছাপা হয়েছে (১৯২১ সালের ৬ জানুয়ারি, ২২ পৌষ ১৩২৮ বঙ্গাব্দ)।মুজফফর আহমদের কথায়, ‘বিদ্রোহী’ প্রথম ছাপানোর সম্মান বিজলীরই প্রাপ্য।’ এ কথা অবশ্য ঠিক যে ‘মোসলেম ভারতে’ প্রকাশের জন্য নজরুল ‘বিদ্রোহী’ কবিতা সম্পাদক আফজালুল হককে প্রথমে দিয়েছিলেন। কিন্তু ‘মোসলেম ভারতে’র কথিত সংখ্যাটি বের হতে দেরি হয়ে গিয়েছিল।’এরপর মাসিক ‘মোসলেম ভারত’ পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় (পত্রিকাটি অনিয়মিত হওয়ায় বাংলা ১৩২৮ সালের কার্তিক মাসের পরিবর্তে মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল) ‘বিদ্রোহী’ কবিতাটি আবারও ছাপা হয়। একই বছর এটি মাসিক ‘প্রবাসী’ এবং মাসিক ‘বসুমতী’ এবং পরের বছর (১৩২৯ সালে) মাসিক ‘সাধনা’য় পুনঃপ্রকাশিত হয়।
তারপর ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসে প্রকাশিত নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘অগ্নিবীণা’য় এটি আরো ১২টি কবিতার সাথে স্থান পায়। ‘অগ্নিবীণা’ প্রকাশ করেছিল কলকাতার আর্য পাবলিশিং হাউস।এর প্রচ্ছদ পরিকল্পনা করেছিলেন কবিগুরুরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাই’পো অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অংকন করেছিলেন শিল্পী বীরেশ্বর সেন। ‘অগ্নিবীণা’ এতোই জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রকাশের সাথে সাথেই এর প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং তারপর আরো কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছিল। বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন কবিতা-সম্বলিত ‘অগ্নিবীণা’ বাংলা সাহিত্যের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল।‘বিদ্রোহী’ কবিতা ও ‘অগ্নিবীণা’ কাব্যগ্রন্থের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা তখন বেরিয়েছিল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায় পাতায় এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মত লেখকদের লেখায় লেখায়।
কবিতাটি প্রকাশ হওয়া মাত্র এমনই জনপ্রিয় হয় যে, একই সপ্তাহে প্রকাশকরাসংশ্লিষ্ট পত্রিকার কয়েকটিসংস্করণ বের করতেবাধ্য হন। ‘বিদ্রোহী’ কবিতার এই পুনঃ পুনঃ প্রকাশনা তখনকার সময়ে পাঠক ও প্রকাশকের মধ্যে এর তুমুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ বহন করে। বস্তুত এই কবিতার জন্ম বাংলা সাহিত্য ও বাঙালির সংগ্রামের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত সাড়া জাগানো ঘটনা। পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকা, ব্রিটিশরাজের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী বাঙালি জাতিকে নজরুল এ কবিতার মাধ্যমে ভীষণভাবে নাড়া দিয়েছিলেন।বিশেষ করে মুক্তিকামী বাঙালি তরুণ সমাজের কাছে এ কবিতা ছিল রক্তে উন্মাদনা সৃষ্টিকারী, হৃদয়ে অগ্নি-প্রজ্বলনকারী এক বজ্রকঠিন বার্তা। তাদের হয়ে যেন নজরুল বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন:
আমি বেদুঈন, আমি চেঙ্গিস
আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ!
নজরুলের এই রুদ্ররোষ যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল, তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকার-কর্তৃক তাঁর একাধিক প্রকাশিত গ্রন্থ বাজেয়াপ্তকরণ ও তাঁকে কারাদণ্ড প্রদান তারই প্রমাণ।
অপরদিকেবিদ্রোহী প্রকাশের পরপরই মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে কঠোর সমালোচনা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। মুসলিম সমাজ নজরুলের বিরুদ্ধে মৌখিক ও লিখনীর মাধ্যমে উঠে পড়ে লাগে। তাদের মতে, নজরুল ধর্মদ্রোহী হয়ে গেছেন। তিনি ইসলাম ধর্মের অবমাননা করেছেন। বিদ্রোহীতে নজরুল লিখেছেন-
‘ভ্যূলোক দ্যুলোক ভেদিয়া
খোদার আসন ‘আরশ’ ছেদিয়া
উঠিয়াছি চির-বিস্ময় আমি বিশ্ব-বিধাত্রীর। ’
মুসলমান সমাজের কঠোর সমালোচনার মধ্যে মুন্শী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদকবির সমালোচনা করে বলেছিলেন, ‘মোসলেম ভারতে বিদ্রোহী কবিতাই কাজীর কারামৎ জাহির হয়েছিল। তারপর ধুমকেতু প্রত্যেক সংখ্যায় পবিত্র ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে গরল উদ্গীরণ করিতেছে। এ উদ্দাম যুবক যে ইসলামী শিক্ষা আদৌ পায় নাই তাহা ইহার লেখার পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে প্রকাশ পাইতেছে। হিন্দুয়ানি মাদ্দায় ইহার মস্তিষ্কপরিপূর্ণ। …নরাধম হিন্দু ধর্মের মানে জানে কি? …এই রূপ ধর্মদ্রোহী কুবিশ্বাসীকে মুসলমান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। (লোকটা মুসলমান না শয়তান?)কবি নজরুল এবরাহিম খাঁর একটি চিঠির উত্তরে মুসলিম সমাজের সমালোচনার উল্লেখ করে লেখেন- ‘মুসলমান সমাজ যে আমাকে কাফের খেতাব দিয়াছে তাহা আমি মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিয়াছি। ইহাকে আমি কোনোদিন অবিচার বলিয়া অভিযোগের বিষয় করি নাই। কারণ আমার আগে ওমর খৈয়াম, শামসুদ্দিন হাফেজ কিংবা মনসুর আল হাল্লাজকেও কাফের বলিয়াছিল। ’
শুধু যে মুসলিম সমাজ কবি নজরুলের সমালোচনা করে তাঁকে কাফের মুরতাদ কিংবা হিন্দুয়ানি আখ্যা দিয়ে বিতর্কিত করেছিল তা নয়- হিন্দু সমাজও তাঁকে ‘সাম্প্রদায়িক’ ও ‘উগ্রমুসলমান’ বলে আখ্যা দিয়েছিল।কবি নজরুল দুঃখ পেয়ে লিখেন- ‘কয়েকজন গোড়া ‘হিন্দুসভা’ওয়ালা তাহার নামে মিথ্যা কুৎসাও রটনা করিতেন। ইহাদিগকে আঙ্গুল দিয়া গণনা করা যায়, ইহাদের আক্রোশ সম্পূর্ণ সম্প্রদায় বা ব্যক্তিগত। আজকালকার সাম্প্রদায়িক মাতলামির দিনে, আমি যে মুসলমান ইহাই হইয়া পড়িয়াছে অনেক হিন্দুর কাছে অপরাধের সামিল আমি যতো বেশি অসম্প্রদায়িক হই না কেন?’
তৎকালীন হিন্দু লেখকসমাজ কবি নজরুলের ‘বিদ্রোহী’র আরবি, ফার্সি শব্দের সাথে সংস্কৃত শব্দের মিলবন্ধনকে মেনে নিতে পারেনি। মেনে নিতে পারেনি বিদ্রোহীর দ্রোহ ভরা চরণগুলোকে। কবি তাঁর দ্রোহের প্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে-আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দিব পদ-চিহ্ন!
আমি খেয়ালি বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন।
বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম অন্য স্থানে চরণ জুড়ে দেন-
‘আমি মানব দানব দেবতার ভয়,
বিশ্বের আমি চির-দুর্জয়।
জগদ্বীশ্বর ঈশ্বর আমি পুরুষোত্তম সত্য
আমি তাথিয়া তাথিয়া মাথিয়া ফিরি এ স্বর্গ-পাতাল-মর্ত্য!’
‘বিদ্রোহী’ কবিতা মুসলিম এবং হিন্দু সমাজে সমালোচনা সৃষ্টিকরলেও সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ব্রিটিশ শাসিত পুরো উপমহাদেশে। কবিতাটি নাড়িয়ে দিয়েছিল ব্রিটিশ শাসনের ভিত।















